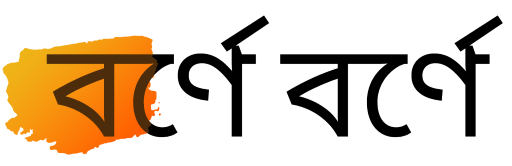জয়পুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার বনাঞ্চল ও ইতিহাসের জোড়া হাতছানি
শাশ্বত বোস,
মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী
ভ্রমণ, মানে যাকে বলে ঘুরতে যাওয়া, শুনলেই মনের ভেতরটা কেমন যেন নেচে ওঠে
না? এই যে আমি, প্রায় মধ্য যৌবনে পৌঁছে গেছি। এই আমারই হয় ভীষণভাবে হয়।
মনে হয় কিছু একটা অজানা অদেখা যেন আড়াল থেকে আমাকে দেখছে, নজর রাখছে। ঠিক
যেই মুহূর্তে তার সাথে আমার দেখা হবে অমনি প্রচন্ড আলোর দ্যুতি নিয়ে সে
আমায় জড়িয়ে ধরবে। অবশ্য ছোটবেলায় আমি যে হাওড়া-কলকাতা মাসি আর পিসি বাড়ি
যেতাম, ওই বয়সে সেটাই আমার জগৎ ছিল। সেখানে গেলে একটা ভীষণ ভালো লাগা
আমাকে আঁকড়ে ধরতো। তবু বেড়াতে যাওয়া বিষয়টা যে বেশ খানিকটা পরিব্যাপ্ত
একটা বিষয়, ইন্দ্রিয় আর মস্তিষ্কের অনেকখানি জুড়ে যে তার প্রসার, সেটা
বুঝতে পারতাম বেশ, ওই বয়স থেকেই। যে জায়গাটায় বেড়াতে যাব, হতে পারে তার
নৈসর্গিক বৈচিত্র নয়নাভিরাম সম্মোহন এনে দেয় দৃশ্যের গহীন প্রসারতায়!
হয়তো বা সে দৃশ্য শান্ত সমাহিত। হয়তো সেখানে পাহাড়ি রাস্তার ঢালে উঁচু
উঁচু গাছগুলো আকাশ ছুঁতে চায়। হয়তো বা পাহাড়ি ঝর্ণা সেখানে কোন নির্জনতার
বোধ নিয়ে দামাল বেগে ঝাঁপিয়ে পরে, অপার জ্যোৎস্নাকে বুকে করে। হয়তো বা
উৎসব মুখর সমুদ্রস্নানে পড়ন্ত সূর্য্যটা একমুঠো রাঙা আবির মেখে
বালুকাবেলায় একই সাথে সুন্দর আর ভয়ঙ্করের হড়পা বান ডেকে আনে। কখনও বা সেই
দৃশ্যকল্প ছড়িয়ে পরে অরণ্যের গভীরে। ছায়াময়তা আর অদৃশ্য আলোর অচেনা
প্যাটার্ন সাজিয়ে রাখে মাথার ওপরের তারাদের জগৎ। কয়েকশত আলোকবর্ষ ছাড়িয়ে
যায় সেই তরঙ্গস্নান। ক্যালাইডোস্কোপের অনন্ত বর্ণালীর মত ছড়িয়ে গিয়ে আবার
জড়ো হয়ে যাবার মত এই ভাবনাগুলো কেমন যেন তখন পেয়ে বসে আমাকে।
এবারে ভ্রমণের গন্তব্য হিসেবে আমি বেছে নিয়েছিলাম বাঁকুড়া জেলার শরীর
বেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জনপদগুলোকে, তার প্রাকৃতিক সুন্দরতা এবং
জায়গাগুলো জুড়ে গড়ে ওঠা সীমিত জনবসতির মাঝে আদিম ও বর্তমানের যৌথজীবনকে,
সম্পর্কের মায়াদর্পণে ভালোভাবে ঝালিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। কলকাতা থেকে
প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দূরত্ত্বে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তের
জেলাগুলোর অন্যতম একটি হল এই বাঁকুড়া। সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য এবং
সবুজ বনাঞ্চলের সাথে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে এক অন্য মাত্রা এনে দেয় বাঁকুড়ার
পাহাড়। এবার আসা যাক বাঁকুড়ার কিছু অন্যতম দর্শনীয় স্থান প্রসঙ্গে।
জয়পুর ফরেস্ট, বিচিত্র বনানী ও জংলী জীবজগতের এক মধুর সমাপতন
দু পাশে সারি সারি শাল, সেগুন, বহেড়া, মহুয়া গাছ মাঝে এক চিলতে পিচ
রাস্তা। তাও আবার জায়গায় জায়গায় এলিফ্যান্ট করিডোর এবং ডিয়ার প্যাসেজ! সব
কটি গাছই যেন মহীরুহে পরিণত হয়েছে। মাথার দিকে গিয়ে জড়ো হয়ে তৈরী করেছে,
ভেজা ভেজা নরম এক সামিয়ানা। জঙ্গলের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে! হয়তো বা সেই
গন্ধ জায়গায় জায়গায় ফিরোজা রঙের আনন্দ বয়ে আনে। জঙ্গলের মাঝের সেই পথে
কোথাও কোন দেবদূত আগলে নেই, কোথাও জীবন চালনায় এতটুকু ত্রুটি নেই! সেখানে
দিনের ওপর চেপে বসে থাকে ভারী একটা রাত। রাতের কোল জুড়ে খেলা করে সদ্য
পূর্ণিমা থেকে সরে আসা হিম জোছনা! জীবন যেন এখানে প্রবলভাবেই একমুখী।
এখানে জঙ্গল জুড়ে বাস হাতি, চিতল হরিণ, বুনো শেয়াল, বুনো শুয়োর ছাড়াও
ময়না, দূর্গা-টুনটুনি সহ আরো অন্যান্য বহু দেশী বিদেশী পাখির।
স্থানীয়ভাবে এটি একটি পিকনিক স্পট হলেও জঙ্গলের মধ্যে নিশিযাপনের জন্য
কিংবা একদিনের ঝটিতি সফরের মাঝে দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য রয়েছে ‘বনলতা
ইকো টুরিজম রিসর্ট’ এর মত অত্যাধুনিক অথচ মাটির কাছাকাছি ধুলো গন্ধ মেখে
তৈরী হওয়া সাকিনটি। জঙ্গলের ভেতর আরেকটি দেখবার মত জায়গা হল,
‘অ্যারোডোম’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরী কংক্রিটের এই রানওয়ে, মূলত
রয়েল এয়ার ফোর্সের যুদ্ধ বিমান ওঠানামার জন্য বানানো হয়েছিল। কোন অদৃশ্য
জাদুবলে কিংবা কারিগরীর আধুনিকতায় এটি জায়গায় জায়গায় আজও অটুট আছে!
জঙ্গলের মাঝের আঁকা বাঁকা মেঠো পথ ধরে এগোলে পড়বে একটি পরিত্যক্ত রেললাইন
ও একটি ওয়াচ টাওয়ার। পাশ দিয়ে দ্রুতগামী বাতাসের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে
বয়ে চলেছে একটি ক্যানেল, যা নাকি অনতিদূরে কংসাবতীতে গিয়ে মিশেছে। এটি
দেখে হলিউডের বিখ্যাত থ্রিলার মুভি ‘হাউল’ এর কথা মনে পড়তে বাধ্য! হয়তো
এই লাইন বেয়েই শেষের ট্রেন চলে গেছে একটানা একটা দীর্ঘ্য হুইসেল দিয়ে।
তারপরেই পড়েছে কোন অশরীরী নেকড়ের দলের কবলে! যদি এই কাল্পনিক ভয়ের
দৃশ্যটির রেশ কাটিয়ে ওঠা যায় আদৌ, তাহলে পরিতক্ত্য ওয়াচ টাওয়ার থেকে পুরো
জঙ্গলটাকে শান্ত চোখে দেখে নেওয়া যেতেই পারে। নির্জনতার সংকেত বয়ে নিয়ে
আসা বুনো গন্ধটা শরীরে মেখে নিলে চোখে পড়তেই পারে জঙ্গলের বুক চিরে
বেরিয়ে আসা একটা ত্রস্ত হাতির পাল কিংবা অনিয়ন্ত্রিত ফাল্গুনের দিকে ছুটে
যাওয়া হরিনের দলের গতিবিধি! যা মুহূর্তে চঞ্চল করে দিতে পারে মনটাকে।
বিষ্ণুপুর, মহাকাব্যের পাতা থেকে উঠে আসা মন্দিরের সমারোহ তীর্থ
বাঁকুড়া জেলার অবস্থান ঠিক মধ্য রাঢ়ে! এই রাঢ়ভূমি কিন্তু বিস্তৃত গঙ্গার
পশ্চিম উপকূল থেকে মানভূমের পাদদেশ অবধি। সুতরাং চিরসবুজ শ্যামলিমা আবার
উষর রুক্ষতা এই চিরবিবাদী ভৌগোলিক বৈপরীত্যই বাঁকুড়া জেলাকে আরো মোহময়ী
করে তোলে। বিষ্ণুপুর এক ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান, একদা বাংলার গৌরব। বাঙালি
বীরের শৌর্য্য ও বীর্য্যের লীলাভূমি! পূর্ব ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির
প্রাণকেন্দ্র মল্লভূমের রাজধানী ছিল এই বিষ্ণুপুর (মল্লবাণী)। বর্তমানে
বাঁকুড়া জেলার একটি সামান্য মহকুমা শহর এই বিষ্ণুপুর কিন্তু ইতিহাস থেকে
জানা যায় পূর্বকালে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর, হুগলীর আরামবাগ হয়ে
হাওড়া, পশ্চিমে ছোটনাগপুর, দক্ষিণ মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর তমলুক ও
উত্তরে দামোদর নদ, আসানসোল পর্যন্ত্য ছিল এই মল্লভূম রাজ্যের বিস্তৃতি।
আদিবাসী রাজ্য ধলভূম, টুংভূম, সামন্তভুম, বরাহভূমও ধীরে ধীরে বিষ্ণুপুরের
রাজাদের অধীনস্থ হয়। এই মল্লরাজবংশের আদিতম রাজা আদি মল্লের
পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত আসেন রাজপুতানা থেকে। বিষ্ণুপুরের প্রধান দ্রষ্টব্য
টেরাকোটার মন্দিরগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে মল্ল রাজবংশের কিছু
উল্লেখ্য বীর যোদ্ধা ও তাদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনার
প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। তাতে নিছক ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি ইতিহাসের
গায়ের ভিজে গন্ধটাও কিছুটা নাকে এসে লাগে।
দীর্ঘ্য শতাব্দী ধরে বিষ্ণুপুরের রাজারা নিজেদের শাসনকার্য্যে অটল ছিলেন।
পরবর্তীকালে মুঘল শক্তি প্রসারিত হলে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে মুসলমানি প্রভাব
বাড়তে দেখা যায়। তবুও তা ছিল সম্প্রীতির এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিষ্ণুপুরের
অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মোগলরা কখনোই হস্তক্ষেপ করতেন না। মল্ল রাজবংশের আদি
মল্ল লোগ্রামে তেত্রিশ বছর রাজত্ত্ব করেছিলেন এবং বাগদি রাজা নাম পরিচিত
ছিলেন। তাঁর পুত্র জৌ মল্ল নিজের রাজ্য প্রসারিত করেন ও তাঁর রাজধানী
বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত করেন। এই মল্ল রাজবংশের উনপঞ্চাশতম শাসক বীর
হাম্বির যিনি আনুমানিক পনেরো শতকের দিকে বিকাশ লাভ করেন, পরবর্তীতে
শ্রীনিবাসের ভাগবত পাঠে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত
হন। তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে রঘুনাথ সিংহই প্রথম সিংহ পদবী ব্যবহার
করেন। কথিত আছে মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।
রঘুনাথ সিংহ ১৪৩৩ থেকে ১৫০৬ অব্দের মধ্যে ‘শ্যাম রাই’, ‘জোড় বাংলা’ ও
‘কালাচাঁদ’ মন্দির নির্মাণ করেন। বীরসিংহ বর্তমান দুর্গটি ১৬৫৮ সালে
নির্মাণ করেন সাথে নির্মাণ করেন ‘লালজি মন্দির’, ‘লালবাঁধ’, ‘কৃষ্ণবন্ধ’,
‘গানতবন্ধ’, ‘যমুনবন্ধ’, ‘কালিন্দীবন্ধ’, ‘শ্যামবন্ধ’ ও ‘পোকবন্ধ’ নাম
সাতটি বড় হ্রদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তার রানী শিরোমনি বা চূড়ামণি ১৬৬৫
সালে ‘মদনমোহন’ ও ‘মুরালিমোহন’ মন্দিরটি নির্মাণ করান। বিষ্ণুপুরের
মন্দিরগাত্রে ফুটিয়ে তোলা টেরাকোটা শিল্পে পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ দশাবতার ও
শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত আছে। স্থাপত্যের ও ধর্মীয় ভাবাবেগের নিদর্শন হিসেবে
গড়ে ওঠা মন্দিরগুলোর গায়ে কান পাতলে আজও হয়তো শোনা যাবে ইতিহাসের
ফিসফিসানি। এখানকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মন্দির ও স্থাপত্য সম্পর্কে কিছু
আলোকপাত করার চেষ্টা করলাম।
রাসমঞ্চ
রাসমঞ্চ বিষ্ণুপুর শহরের একটি পুরাতাত্ত্বিক স্থাপনা। মল্লরাজা বীর
হাম্বীর আনুমানিক ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে এই মঞ্চটি নির্মাণ করেন। বৈষ্ণব রাস
উৎসবের সময় বিষ্ণুপুর শহরের যাবতীয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এখানে জনসাধারণের
দর্শনের জন্য আনা হত। ১৬০০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এখানে রাস উৎসব আয়োজিত
হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য এখানে আর উৎসব হয় না।
স্থাপত্যশৈলী
রাসমঞ্চ একটি অভিনব স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন। মঞ্চের বেদিটি মাকড়া বা
ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত। বেদিটির উচ্চতা ১.৬ মিটার ও দৈর্ঘ্য ২৪.৬
মিটার। মঞ্চটির মোট উচ্চতা ১০.৭ মিটার। উপরের অংশ ইষ্টকনির্মিত। চূড়ার
কাছে একটি স্বল্প পরিসর ছাদে গিয়ে উপরের অংশটি মিলিত হয়েছে।
রাসমঞ্চের চূড়া পিরামিডাকৃতির। চূড়ার মূলে চারটি করে দোচালা ও প্রতি
কোণে একটি করে চারচালা রয়েছে। গর্ভগৃহটি দেওয়াল-দ্বারা আবৃত নয়। বরং
রাসমঞ্চের গর্ভগৃহটিকে ঘিরে রয়েছে তিন প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল।
বাইরের সারিতে খিলানের সংখ্যা ৪০। এই খিলানগুলির গায়ে পোড়ামাটির পদ্ম ও
পূর্ব দেওয়ালে বিষ্ণুপুরের গায়ক-বাদকদের স্মৃতি-অলংকৃত কয়েকটি
টেরাকোটার প্যানেল রয়েছে। রাসমঞ্চটি বিষ্ণুপুরের প্রচলিত স্থাপত্যরীতি
অনুসরণে নির্মিত হয়নি।
কেষ্ট রায় মন্দির
কেষ্ট রায় মন্দির, যা জোড়-বাংলা মন্দির নামেও পরিচিত, বিষ্ণুপুর শহরের
একটি কৃষ্ণ মন্দির। অতীতে, এই মন্দিরে হিন্দু দেবতা কৃষ্ণকে ‘কেষ্ট রায়’
রূপে পূজার্চনা করা হলেও বর্তমানে কোনো পূজা করা হয় না। মন্দিরে প্রাপ্ত
প্রতিষ্ঠা ফলক অনুযায়ী, মন্দিরটি ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে (৯৬১ মল্লাব্দে)
মল্লভূমের রাজা রঘুনাথ সিংহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরটি
জোড়-বাংলা মন্দিরের স্থাপত্যের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ, যা মধ্যযুগীয়
বাংলায় বিকশিত চালা শৈলীর অন্তর্গত।
মন্দিরটি বাংলার সর্বপ্রাচীন একটি জোর-বাংলা মন্দির। এটি সম্ভবত বাংলার
সবচেয়ে পরিচিত টেরাকোটা মন্দির। বর্তমানে এটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব
সর্বেক্ষণ দ্বারা ভারতের অন্যতম একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে
সংরক্ষিত রয়েছে।
স্থাপত্য
কেষ্ট রায় মন্দিরে চালা শৈলীর একটি শ্রেণি জোড়-বাংলা ও রতন শৈলীর
সমন্বয় দেখা যায়, তবে মন্দিরটি মূলত জোড়-বাংলা স্থাপত্য শৈলীতে
নির্মিত। মন্দিরের কাঠামোটি দো-চাল রীতিতে নির্মিত দুটি ঘর ও একটি রত্ন
সহযোগে গঠিত। মন্দিরটিতে ঢালু ছাদ ও প্রাথমিক চালা শৈলীর উপাদানগুলি
দেখতে পাওয়া যায়, যা এই সময়ে নির্মিত বাংলার হিন্দু মন্দিরগুলির সাধারণ
বৈশিষ্ট্য ছিল। মন্দিরের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর ভারতীয় পুরাতত্ত্ব
সর্বেক্ষণ দ্বারা সুন্দরভাবে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত করা হয়েছে।
বহির্ভাগ
মন্দিরটি হল একটি রত্ন সহ জোড়-বাংলা মন্দির, যেখানে দুটি দো-চালা কাঠামো
একত্রে মিলিত হয়ে একক নিরবিছিন্ন চালা গঠন করেছে এবং দো-চালা কাঠামো
দুটির সংযোগস্থলের উপরে চালা শৈলীতে নির্মিত একটি রত্ন রয়েছে। দক্ষিণ
দিকের চালাটি মণ্ডপ হিসেবে কাজ করে এবং উত্তর দিকের চালাটি গর্ভগৃহ
হিসাবে কাজ করে। মন্দিরটি পাথর নির্মিত একটি মঞ্চের উপর নির্মিত
হয়েছে।
মন্দিরের তিনটি খিলানাকার প্রবেশ পথ রয়েছে, যেগুলো ৪ টি স্তম্ভের
সাহায্য নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরের উত্তর দিকের দেয়ালে ৪ টি স্তম্ভ
সমর্থিত তিনটি খিলান রয়েছে, তবে খিলানগুলি ভিতর দিক থেকে ছদ্ম দেওয়াল
দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া আছে। উত্তর দিকের দেয়ালে খিলানগুলি প্রবেশপথ বা
প্রস্থানপথ হিসাবে নয়, বরং দক্ষিণ দেয়ালের সাথে ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবে
মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছিল। খিলান গঠনকারী
স্তম্ভগুলি ব্যতীত মন্দিরের দেয়ালগুলির বহির্ভাগে অপেক্ষাকৃত কম
ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ১৬ টি স্তম্ভ প্রথিত রয়েছে। এছাড়া, দক্ষিণ ও উত্তরের
খিলানগুলির উপরে দুটি করে মোট ৪ টি স্তম্ভ দেয়ালে প্রথিত রয়েছে। দূর
থেকে দেখে মনে হয় যেন অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসার্ধের স্তম্ভগুলি ছাদের
(চালা) কার্নিশকে ধরে রেখেছে।
দো-চালা ঘর দুটি অর্থাৎ মণ্ডপ ও গর্ভগৃহের চালা বা ছাদ পরস্পরের সঙ্গে
সংযুক্ত থাকলেও, গঠনগতভাগে দেয়াল দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়।
মণ্ডপ ও গর্ভগৃহের দেয়ালের মাঝে ০.৭৫ মিটার (২.৫ ফুট) এর ফাঁক
রয়েছে।
ছাদ গঠনকারী দুটি চালার শীর্ষভাগের মাঝে যে উপত্যকা সেই উপত্যকার উপরে ইট
দ্বারা নির্মিত একটি বর্গাকার মঞ্চ রয়েছে, যার উপরে একটি রত্ন রয়েছে।
চার-চালা বিশিষ্ট রত্নটি চালা শৈলীতে নির্মিত।
অভ্যন্তর
মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তিনটি খিলানাকার প্রবেশ পথ রয়েছে,
যেগুলি দক্ষিণমুখী সম্মুখভাগে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ দুটি কক্ষ
নিয়ে গঠিত, যথাক্রমে - মণ্ডপ ও গর্ভগৃহ। প্রবেশপথগুলি মণ্ডপে প্রবেশের
অনুমতি প্রদান করে। ০.৭৫ মিটার (২.৫ ফুট) দূরত্বে থাকা দেয়াল দুটির
প্রতিটিতে একটি করে খিলান রয়েছে, এবং দেয়ালদুটির মাঝে ইটের দেয়াল
রয়েছে; ফলে মণ্ডপ ও গর্ভগৃহ পরস্পরের সঙ্গে মাঝে একটি আবদ্ধ পথ দ্বারা
সংযুক্ত আছে।
শ্যামরায় মন্দির
শ্যামরায় মন্দির বিষ্ণুপুর শহরের অন্যতম একটি পুরাতাত্ত্বিক স্থাপনা।
মন্দিরটি পঞ্চ-রত্ন মন্দির স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত, যা মধ্যযুগীয়
বাংলায় বিকশিত রত্ন শৈলীর অন্তর্গত।
নির্মাণকাল
মন্দিরের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে নিবদ্ধ লিপি থেকে মন্দিরের নির্মাণকাল
সম্বন্ধে জানা যায়। এই লিপিটি নিম্নরূপ,
“শ্রীরাধিকা কৃষ্ণমুদে শকেঙ্ক
বেদাঙ্ক যুক্তে নবরত্নরতং
শ্রীবীর হাম্বীর নরেশ সূনূর্দদৌ
নৃপ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ ।।
মল্ল সকে ।”
এই লিপি থেকে জানা যায় রাধা ও কৃষ্ণের আনন্দের জন্য রাজা বীর হাম্বীরের
পুত্র রাজা রঘুনাথ সিংহ ৯৪৯ মল্লাব্দে বা ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে এই নবরত্ন
মন্দিরটি দান করেন।
স্থাপত্যশৈলী
মন্দিরটি চৌকো, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১১.৪ মিটার। মন্দিরের চারদিকের
খিলানগুলি সুন্দর কারুকার্য্যময় স্তম্ভের ওপর নির্ভর করে নির্মিত হয়ে
ফাঁকা দালানের মতো অংশের সৃষ্টি করেছে। এই দালানের ভেতরে মন্দিরের
গর্ভগৃহটি অবস্থিত। গর্ভগৃহের দরজা টেরাকোটা শৈলীতে ফুল ও বিভিন্ন প্রকার
নকশা দ্বারা সাজানো। মন্দিরের ছাদ চৌকো ও উত্তলাকার। ছাদের চার প্রান্তে
চারটি শিখর বা শীর্ষ বর্তমান। উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত এই
শিখরগুলি প্রত্যেকটি প্রতিসম। ছাদের ঠিক মাঝে একটি অষ্টভূজাকৃতি শিখর বা
গম্বুজ বর্তমান। এই অংশে মন্দিরের উচ্চতা ১০.৭ মিটার। মন্দিরের বাইরের ও
ভেতরের দেওয়ালে রাসলীলা, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী এবং বিভিন্ন
কারুকার্যের দৃশ্য আছে।
মদনমোহন মন্দির
মদনমোহন মন্দির হল বিষ্ণুপুরের অতি প্রাচীন একটি কৃষ্ণ মন্দির। অতীতে, এই
মন্দিরে হিন্দু দেবতা কৃষ্ণকে মদনমোহন রূপে পূজার্চনা করা হলেও বর্তমানে
কোনো পূজা করা হয় না। মন্দিরে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠা ফলক অনুযায়ী, মন্দিরটি
১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে (১০০০ মল্লাব্দ) মল্লভূমের রাজা দুর্জন সিংহ দেব
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরটি একরত্ন মন্দিরের স্থাপত্যের একটি
অনন্য উদাহরণ, যা মধ্যযুগীয় বাংলায় বিকশিত রত্ন শৈলীর অন্তর্গত।
এই মন্দিরটির ছাদ চৌকো ও বাঁকানো, কিনারা বাঁকযুক্ত ও মধ্যে গম্বুজাকৃতি
শীর্ষ বর্তমান। মন্দিরটি অলংকরণের জন্য অনেক বেশি পরিচিত, অলঙ্করণগুলি
প্রধানত দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের উপর স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরের
দেওয়ালে কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্য
ভাস্কর্যের মাধ্যমে রূপায়িত। মন্দিরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১২.২ মিটার এবং
উচ্চতা ১০.৭ মিটার।
বর্তমানে মন্দিরটি এটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ দ্বারা অন্যতম একটি
প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষিত রয়েছে।
ইতিহাস
বিষ্ণুপুরের ৫৫ তম রাজা শ্রী গোপাল সিংহ ছিলেন মদনমোহনের একনিষ্ঠ ভক্ত।
এসময় মারাাঠা দস্যুরা ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে এক লক্ষ সেনা নিয়ে
বিষ্ণুপুর আক্রমণ চেষ্টা করলে রাজা সমরসজ্জায় দৃষ্টি না দিয়ে প্রজাদের
মদনমোহনের উপাসনা করার নির্দেশ দেন। কথিত আছে মদনমোহন নিজহস্তে কামানের
তোপ বর্ষণ করে বিষ্ণুপুর কে রক্ষা করেন। যদিও ঐতিহাসিকেরা এই কিংবদন্তির
সাথে সহমত নন তাদের মতে বিষ্ণুপুরের দুর্গ সেসময় অত্যন্ত দৃঢ় ছিল যা
ভেদ করা মারাঠা দস্যু দের পক্ষে সম্ভব হয়নি।
বিষ্ণুপুরের ৫৬তম রাজা চৈতন্যদেবের আমলে ব্রিটিশের চক্রান্তে বিশাল
রাজস্ব দেনায় রাজা অষ্টধাতুর মদনমোহন বিগ্রহ বন্ধক রাখেন। এভাবে মদনমোহন
বিগ্রহ হাতছাড়া হয়। বর্তমানে বাগবাজার মদনমোহন মন্দিরে এই মূর্তি
অধিষ্ঠান রত।
স্থাপত্য
মদনমোহন মন্দির বাংলার মন্দির স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটি
একটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আয়তকার প্রাঙ্গণ নিয়ে গঠিত। প্রাঙ্গণে
মুখ্য দেবালয়, ভোগমণ্ডপ ও নাটমন্দির রয়েছে। মুখ্য দেবালয়ে বাংলার
বিখ্যাত রত্ন শৈলী দেখা যায়। এটি একরত্ন শৈলীতে নির্মিত। মন্দিরের
কাঠামোটি বাঁকানো ছাদ সহ ঘর ও একটি রত্ন সহযোগে গঠিত। ভোগমণ্ডপ ও
নাটমন্দির চালা শৈলীতে নির্মিত হয়েছে, এবং পশ্চিম দিকের প্রাচীর সঙ্গে
চালা শৈলীতে নির্মিত একটি তোরণ রয়েছে। মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব
সর্বেক্ষণ দ্বারা সুন্দরভাবে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত করা হয়েছে।
মুখ্য দেবালয়
মন্দিরটি পাথর নির্মিত একটি মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যার দৈর্ঘ ও
প্রস্থ উভয়ই ১২.২ মিটার (৪০ ফুট)। মন্দিরের মেঝের পরিমাপ হল ১৪৮.৮৪
মিটার (১৬০০ বর্গফুট) এবং দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ১.৪ মিটার
(৪ ফুট ৭ ইঞ্চি) উচ্চতার মাকড়া-পাথরের ভিত্তিবেদীর ওপর স্থাপিত মন্দিরের
উচ্চতা ১০.৭ মিটার (৩৫ ফুট)।
সম্মুখভাগ
মন্দিরের দ্বারপথটি দক্ষিণমুখী, দ্বারপথ তিনটি খিলান নিয়ে গঠিত। তিনটি
খিলানযুক্ত প্রবেশপথের উপরে, জ্যামিতিক নকশার একটি বিস্তৃত দল একটি
এলাকাকে চিত্রিত করে, যা কেন্দ্রীয় দৃশ্য হিসাবে প্রদর্শিত হয়।
সমরনায়ক ব্যক্তিগণ ধনুক ও তীর নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি যুদ্ধের ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে আছেন। যোদ্ধাদের এই ভিড়ের মধ্যে একটি অনুভূমিক চিত্রে দেখানো
হয়েছে, তীর শয্যায় মৃত্যুবরণ করছেন ভীষ্ম, এটিই মহাভারতের চূড়ান্ত
যুদ্ধ হিসাবে ধরে হয়।
লালজি মন্দির
মল্ল বংশের ৫২ তম শাসক রাজা বীর সিংহ দেবের শাসনকালে (১৬৫৬-১৬৮২) এই
মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমময় মূর্তির
উদ্দেশ্যে সমর্পিত। নীচু খিলান যুক্ত ছাত ও তাতে অনবদ্য stucko কারুকার্য
এবং সেইসাথে ল্যাটেরাইট পাথরের নির্মাণ শৈলী এই মন্দিরের বিশেষ
বৈশিষ্ট্য।
দলমাদল কামান
দলমাদল কামানটিকে ঘিরে একটি বড় অদ্ভুত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মারাঠা
সেনাপতি রঘুজী ভোঁসলে ও তাঁর অন্যতম দক্ষ সেনাপতি ভাস্কর রাওয়ের হাত ধরে
মহারাজা গোপাল সিংহ দেবের আমলে বিষ্ণুপুর ভয়ংকর বর্গী আক্রমণের মুখে পড়ে।
কিন্তু মহারাজা গোপাল সিংহ ছিলেন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে
প্রভু মদনমোহন জিউলের প্রতি ভরসা রেখে নাম-গান সংকীর্তনে মগ্ন হতে বলেন।
এই সময় মদন মোহন মন্দিরের পুরোহিত এসে রাজাকে খবর দেন কিছুক্ষন আগে তিনি
মন্দিরের পথে যাচ্ছিলেন, তখন একটি গোয়ালা ছেলে এসে তাঁকে বলে যে, সে
অভুক্ত! পুরোহিতমশাই তাকে মদনমোহনের প্রসাদস্বরূপ ননী খেতে দেন। সেই
রাতেই বিষ্ণুপুরবাসী যখন ভয়ে থরথর তখনই প্রচন্ড কামানের গর্জ্জন শোনা
যায়! পরদিন সকালে বর্গী সেনা পিছু হটে এবং মদনমোহন বিগ্রহের হাতে বারুদ
লেগে থাকতে দেখা যায়। দলমাদলকে খুঁজে পাওয়া যায় লালবাঁধের খাদের বালিতে
প্রোথিত অবস্থায়! আজও স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন যে এই ভয়ংকর কামানটি থেকে
মারাঠা সেনাবাহিনীর হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য সেদিন ভগবান
মদনমোহন স্বয়ং গোলা নিক্ষেপ করেছিলেন!
‘লালবাঁধে আছিল তোপ দলমর্দন।
প্রকান্ড ভয়ালরূপ লৌহ গড়ন।।
হেলায় ধরিয়া তোপে শ্রী মধুসূদন।
বারুদ ঠাসিল তাহে পূর্ণ আশি মণ।।
জ্বালিয়া সে তোপ প্রভু দাগিলেন দেবে।
যেথায় বর্গীদল আগুয়ান সবে।।
তোপ নামে বিকল সবে কাঁপে থরথর।
কতশত শত্রু নামে প্রভু গিরিধর।।’
জনশ্রুতি, লোকপ্রবাদ আর বৈষ্ণব ভক্তিধারা কোথাও যেন মিলে মিশে জন্ম দেয়,
বিস্ফারিত অক্ষিগোলকে বিছিয়ে রাখা গ্রন্থিত ব্রজবুলির!
জিসকি জুবাহ উর্দু কি তরাহ!
রাসমঞ্চের গা বেয়ে তখন গত পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে সবে। জাগতিক সব দোলাচল
ছাপিয়ে সমগ্র চরাচর ঢেকে যাচ্ছে, বহু প্রতীক্ষিত কোন অচেনা পাথরের শরীর
বেয়ে চুঁয়ে পড়া, পাতলা টলটলে মধুর মত, ভাসা ভাসা বসন্তের অধীর অপেক্ষায়!
বিষ্ণুপুর দেখে এবার আশ্রয়ে ফিরে আসার পালা। গাড়ির সাউন্ড সিস্টেমে তখন
বাজছে এক বিখ্যাত উর্দু কবির লেখা, ইন্ডিপপ সুরের “মেরে নাগমা ওহী, মেরে
কলমা ওহী, মেরা নাগমা নাগমা, মেরা কলমা কলমা মেরা।” মনে মনে ভাবি তবলার
উচ্চ মার্গের ঠেকা বা কবরের উদ্দ্যশ্যে পড়া ইসলামী ইষ্ট মন্ত্রের মতোই
পবিত্র এই বিষ্ণুপুরের ভাষা ও সংগীত! বিশাল এই ভূখণ্ডের প্রাচীন এবং মূল
ভাষা অস্ট্রিক (অস্ট্রো-এশিয়াটিক) এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মুন্ডারী,
সাঁওতালি, হো, খেড়িয়া, অসুরী, শবর, মালপাহাড়িয়া ইত্যাদি গোষ্ঠীর ভাষাও এর
সাথে যুক্ত। পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে প্রাচ্যা মাগধীগুচ্ছের মগহী,
ভোজপুরী, মৈথিলী, বাংলা প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্য্য ভাষা। শাস্ত্রীয়
সংগীতের ইতিহাসে বিষ্ণুপুর ঘরানা একটি উজ্জ্বল নাম! বাংলার একমাত্র
নিজস্ব এই ঘরানা মূলতঃ ধ্রুপদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। কথকতা ও কীর্তনই
একসময় এখানকার জনজীবনের একমাত্র উপজীব্য হলেও শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চ্চা
শুরু হয় আদিগুরু রামশংকর ভট্টাচার্য্যের সময়কাল (১৭৬১-১৮৫৩) থেকে।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাসের সময়কাল (১৩৭০ খ্রীস্টাব্দ) থেকে
বিষ্ণুপুর ঘরানার আদি পর্বের সূচনা হয় বলা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গীতগোবিন্দের আদর্শে বাংলা ভাষায় রচিত রাগ তালে নিবদ্ধ রাধাকৃষ্ণ প্রেম
লীলার প্রথম নান্দনিক প্রকাশ। প্রথম কাহিনীকাব্য যা একই সাথে কাব্য ও
গীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট! চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বৈষ্ণবসমাজ কিছুটা
স্তিমিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে মল্লরাজ বীর হাম্বিরের শাসনকালে
(১৫৮৬-১৬২০) শ্রীনিবাস আচার্য্য শাস্ত্রীয় কীর্তন ও কথকতায় রাজসভাকে
মুগ্ধ করলে রাজ আনুকূল্যে বৈষ্ণবধর্মের পুনরুত্থান হয়। শোনা যায় মুঘল
সম্রাট ঔরংজেবের শাসনকালে (১৬৫৯-১৭০৭) ইসলামী কট্টরপন্থা চূড়ান্তরূপ নিলে
বহু গুণী মানুষ তার দরবার ছেড়ে চলে আসেন এই বিষ্ণুপুরে। এঁদের মধ্যে
উল্লেখযোগ্য তানসেনের বংশধর ওস্তাদ বাহাদুর খান এবং মৃদঙ্গবাদক পিয়ার
বক্স। এসময় দিল্লী দরবার ছেড়ে চলে এলে এঁরা বিষ্ণুপুরে তৎকালীন মল্লভূমের
রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের দরবারে সভাগায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন। বিষ্ণুপুর
ঘরানায় তাই কীর্তনের সাথে মিলে মিশে গেছে শাস্ত্রীয় ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদের
স্থিতধী গম্ভীর এক শাশ্বত সত্য। যা ঈশ্বরবন্দনায় উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তার
শীর্ষে পৌঁছায়। পড়ে অবশ্য রামকিশোর ভট্টাচার্যের হাত ধরে এই ঘরানায় এসে
মেশে খেয়াল ও টপ্পাঙ্গের দ্রুত তানের ঠমক। যা তাঁর অন্যতম শিষ্য যদুভট্ট
(যদুনাথ ভট্টাচার্য) এর হাত ধরে জনপ্রিয়তা পায়। শিল্প শিক্ষার হাত ধরে
আসা ভক্তি উন্মাদনা উদ্বেলিত করেছিল বিষ্ণুপুরের আকাশ বাতাসকে। জ্ঞানের
পথ বেয়ে আসা প্রজ্ঞা ও চৈতন্য পরবর্তী জনজীবনে একাধারে কৃষ্ণপ্রেম ও
অপরদিকে ইসলামী শাস্ত্রীয় সংগীতের স্নেহময় এই মেলবন্ধন যেন আজও অনুভব করা
যায় বেশ খানিকটা।
কলকাতা থেকে কিভাবে যাব
সড়কপথে বিষ্ণুপুরের দূরত্ত্ব কলকাতা থেকে প্রায় ১৩২ কিলোমিটার। ট্রাফিক
পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে যাত্রায় প্রায় ৩-৪ ঘন্টা সময় লেগে যেতে পারে।
ট্রেনে কলকাতার হাওড়া জংশন বা শিয়ালদহ থেকে বিষ্ণুপুর রেলস্টেশন অবধি
নিয়মিত রেল পরিষেবা পাওয়া যায়। রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস বা আরণ্যক
এক্সপ্রেসের মত ট্রেনগুলি এই রুটে নিয়মিত চলাচল করে। ট্রেনের টিকিটও সহজে
পাওয়া যায়। টেনে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টা লাগতে পারে গন্তব্য স্টেশনে
পৌঁছতে। এই যাত্রার সব থেকে চিত্তাকর্ষক দিক হল যাত্রাপথের মনোমুগ্ধকর
প্রাকৃতিক শোভা। বিষ্ণুপুর দেখে গাড়ি ভাড়া করে আসা যেতে পারে জয়পুর
ফরেস্ট। তবে কলকাতা থেকে যেতে গেলে এটিই আগে পরে।